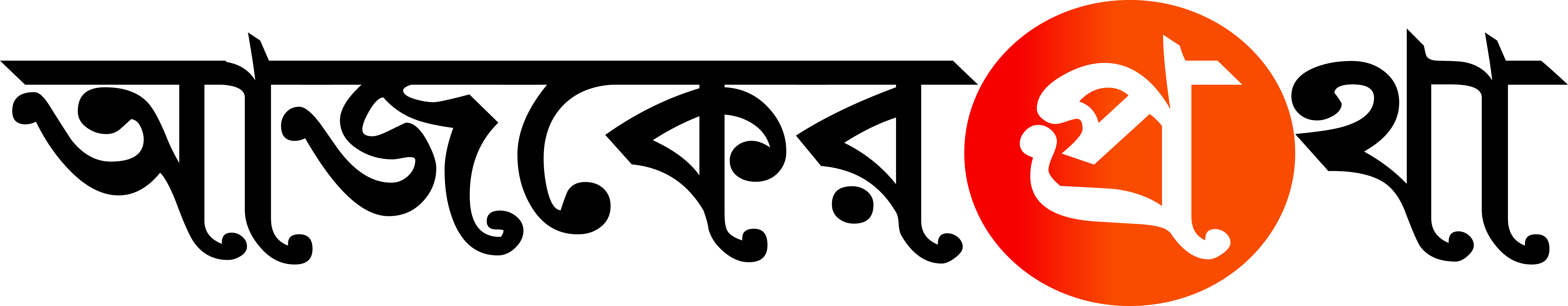পিআর পদ্ধতি নিয়ে রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব


জাতীয় সংসদ । ছবি সংগৃহীত
বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশই জোরালো হচ্ছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকেও পিআর ইস্যুতে দলগুলোর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়নি, যা নির্বাচনী পরিবেশে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।
বিএনপি এই পদ্ধতির ঘোর বিরোধী, তাদের মতে, পিআর আলোচনা আসলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার একটি ষড়যন্ত্র। বিপরীতে, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিসসহ বেশ কয়েকটি দল পিআরকে মানসম্পন্ন নির্বাচনের গ্যারান্টি হিসেবে দেখছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, পিআর পদ্ধতির প্রসঙ্গ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ ও ক্ষমতার ভারসাম্য পুনর্বিন্যাসের একটি কৌশল হতে পারে। তবে মতানৈক্য যেভাবে বাড়ছে, তা আগামী নির্বাচনে নতুন সংকট ডেকে আনতে পারে।
বর্তমান 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরছেন পিআর-সমর্থকরা। তারা বলছেন, একটি দল মোট ভোটের অল্প অংশ পেলেও বিপুল আসন জিতে যায়। ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনের ফলাফল তার উদাহরণ। পিআর চালু হলে প্রতিনিধিত্ব হবে ভারসাম্যপূর্ণ, কোনো দল একক আধিপত্য করতে পারবে না।
অন্যদিকে, বিরোধীরা বলছে, দেশের মানুষ এখনো প্রার্থীভিত্তিক ভোট দেওয়ার অভ্যস্ত। পিআর চালু হলে প্রার্থী নয়, দল নির্বাচন করবে সংসদ সদস্য; এতে জনপ্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা দুর্বল হবে।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, “সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন সাধারণ মানুষ বোঝেই না।” পিআর প্রস্তাবকে ‘ভোট বিলম্বের ষড়যন্ত্র’ বলেও আখ্যা দেন বিএনপি নেতারা।
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, “পিআরে ভোট কারচুপি, কালো টাকা ও পেশিশক্তির জায়গা নেই।” ইসলামী আন্দোলনের নেতারা বলেন, “ফ্যাসিবাদ ঠেকাতে পিআর সবচেয়ে নিরাপদ পথ।”
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রস্তাব করেছে মিক্সড মেম্বার পিআর (MMP) পদ্ধতি—যা প্রচলিত ও পিআরের সংমিশ্রণ।
বর্তমানে ৫০টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে ১৮টি দল পিআর পদ্ধতির পক্ষে, ২৮টি বিপক্ষে এবং ৪টি দল অবস্থান স্পষ্ট করেনি। নিবন্ধনের বাইরেও কিছু দল এই বিতর্কে অবস্থান নিয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, পিআর পদ্ধতি উন্নত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আঞ্চলিক দলের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশে কার্যকর নাও হতে পারে। ফলে বিষয়টি নিয়ে আরও সময় নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা দরকার।